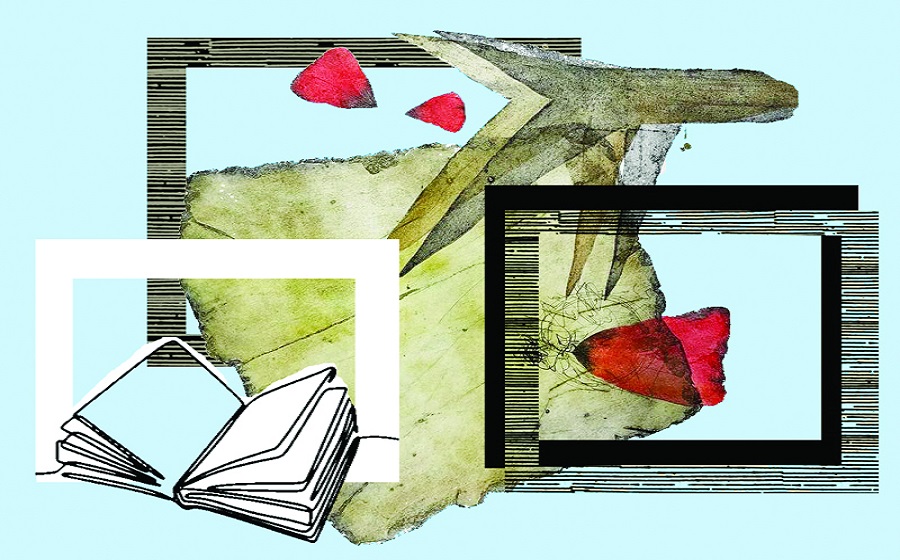 কবিতা কোনো ভাষার অলঙ্কারমাত্র নয়, বরং সেই ভাষার আত্মার সবচেয়ে সূক্ষ্ম, গভীর ও সংবেদনশীল প্রকাশ। বাংলা কবিতা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও বোধের নিগূঢ় নিঃশ্বাস। প্রশ্নটি তাই কেবল সাহিত্যিক নয়, আত্মজিজ্ঞাসার মতোÑ বাংলা কবিতা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, আর আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?
কবিতা কোনো ভাষার অলঙ্কারমাত্র নয়, বরং সেই ভাষার আত্মার সবচেয়ে সূক্ষ্ম, গভীর ও সংবেদনশীল প্রকাশ। বাংলা কবিতা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও বোধের নিগূঢ় নিঃশ্বাস। প্রশ্নটি তাই কেবল সাহিত্যিক নয়, আত্মজিজ্ঞাসার মতোÑ বাংলা কবিতা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, আর আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সময়ের নানা ধাপে, মতবাদে, কণ্ঠে ও সংকটে কবিতার পথরেখা আঁকতে হয়। আমাদের কবিতা কেবল ঐতিহ্যের নয়, বরং প্রতিবাদের, প্রেমের, নিঃসঙ্গতার, এমনকি পরাভব ও পুনর্জন্মেরও ভাষা। তাই এ আলোচনায় বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে বিশ্লেষণ করে একটি স্থিতিবিন্দুতে পৌঁছানো- যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি, আজ কবিতা আমাদের কী বলছে বা বলছে কি আদৌ?
চর্যাপদের আধ্যাত্মিক গূঢ়তা থেকে মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিকতার পাঁজর পেরিয়ে বৈষ্ণবপদাবলির প্রেমঘন ঐকান্তিকতায় বাংলা কবিতার প্রাচীন যাত্রা শুরু। চর্যাপদের ‘আচিন পাখি’ যেমন মানবমনের অচিন অনুভব, তেমনি মধ্যযুগীয় কবিতায় দেব-দেবী, রাধা-কৃষ্ণ, ধর্ম-নীতির অনুরণন- কবিতাকে করেছিল একটি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক অনুরাগের কণ্ঠস্বর। এই সময়ের কবিতায় রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবাদ অনুপস্থিত থাকলেও, ভাষা ও ভাবের যে গভীর স্তর নির্মিত হয়, তা ভবিষ্যতের আধুনিক কবিতার ভিত্তি হয়ে ওঠে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর এ সময়েই বাংলা কবিতা ইতিহাসের গায়ে প্রথম ‘আধুনিকতা’র স্পর্শ পেল। মাইকেল মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ কেবলই একটি কাব্যিক মহাকাব্য নয়, বরং এটি ইউরোপীয় কাব্যচর্চার প্রভাবে উপনিবেশিত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাব্যিক প্রতিক্রিয়া।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কবিতার সবচাইতে বিস্তৃত ও গভীর অধ্যায়- প্রেম, প্রকৃতি, দার্শনিকতা, ব্যক্তিত্ব ও ঈশ্বরবাদ সবই তার কাব্যে অন্তঃস্রোতের ধারায় বহমান। তিনি বাংলাকে একটি আত্মমগ্ন ও স্নিগ্ধ ভাষা দিলেন, যা ‘নিজেকে’ খুঁজতে জানে।
জাতীয়তাবাদী সুর, যা দীনবন্ধু মিত্র বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দের কবিতায় প্রখর হয়ে ওঠে, তা পরবর্তী রাজনৈতিক কবিতার পটভূমি তৈরি করে।
বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কবিতা এক অনন্য বাঁকে এসে দাঁড়ায়- জীবনানন্দ দাশ যেন এই পর্বের নিঃশব্দ কেন্দ্রবিন্দু।
অতীতমুখিতা নয়, বরং সময়ের বহমানতার ভেতর অস্তিত্বের গূঢ় আর্তি। জীবনানন্দের কবিতা আধুনিকতা, নাগরিকতাবোধ ও একাকিত্বের এক অনন্য সেতু- যেখানে ‘শহর’, ‘মানুষ’, ‘স্মৃতি’ ও ‘মৃত্যু’ একটি জটিল কাব্যিক চিত্র হয়ে ওঠে।
কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় যেন আগুনের মতো প্রবেশ করেন তার অগ্নিবীণা কাব্য নিয়ে। ‘ধ্বংস’ এবং ‘নূতন’-এর দ্বৈততা বাংলা কবিতাকে আত্মসম্মান, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যের পথে যুক্ত করে। নজরুল কেবল রাজনৈতিক নন, প্রেম ও রসেরও চূড়ান্ত রূপকার। অন্যদিকে, সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন শ্রেণিসংগ্রামের এক রুদ্র বালককণ্ঠ। সাম্যবাদ, বিপ্লব ও শ্রমজীবী মানুষের আকুতি সুকান্তকে এক অনন্য উচ্চতায় স্থান দেয়।
স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ- এই দুই ঐতিহাসিক বিপর্যয় ও বিজয় বাংলা কবিতায় যে অভিঘাত এনেছে, তার প্রভাব অতল। কবিতা আর নিছক নান্দনিক শিল্প নয়, বরং রাজনীতি, আত্মপরিচয়, শোক ও উত্তরণের ধারক হয়ে ওঠে।
দেশভাগের অভিঘাতে কবিতা যেমন হয়ে ওঠে ভেঙে যাওয়া ভূগোলের কান্না, তেমনি একটি জাতিসত্তা রচনার ভাষা। এই সময়েই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গদ্যসংলগ্ন উচ্চারণে নিয়ে এলেন কবিতার নতুন সংবেদনÑ তার ভাষা কঠিন, অথচ এক পরিশীলিত নাগরিক মননের প্রতীক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জয় গোস্বামী- এঁরা গড়েন আধুনিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাব্যপ্রবাহ।
আত্মসন্ধান, প্রেম, নগরজীবন, দেহ, ভাষার অভ্যন্তরীণ সংগীত- এইসব বিষয় হয়ে ওঠে প্রধান।
আল মাহমুদ, অন্যদিকে, ফিরে যান ইতিহাসের দিকে- ‘আমাদের বুকের ভিতরে হেঁটে যায় কাসেমের জুতো’Ñ এটি কেবলই একটি পঙক্তি নয়, বরং প্রান্তিক ইতিহাসের আত্মপরিচয়।
শামসুর রাহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ের আধুনিক কণ্ঠস্বর- ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা’, শামসুর রাহমানের কবিতায় ভাষা ও প্রতিবাদ সমান্তরাল পথে চলে। তার পাশাপাশি নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী- এইসব কণ্ঠ কবিতায় এক বাস্তবতা ও উত্তরের স্বর এনে দেয়।
আশির দশকে কবিতার অভিমুখ আরো অভ্যন্তরমুখী হয়। রাষ্ট্র ও আদর্শের ব্যর্থতায় কবি ফিরে যান স্বচেতনার গহ্বরে।
জয় গোস্বামীর কবিতা হয়ে ওঠে ঘুমন্ত স্বপ্নের মতো, যেখানে ঈশ্বর, দেহ, ক্ষুধা ও প্রেম একে অন্যের প্রতিবিম্ব।
১৯৯০-এর পর বাংলা কবিতা প্রবেশ করে উত্তরাধুনিক অধ্যায়ে। এখানে সত্য আর একমাত্র নয়, বরং বহুস্বর। নির্মাণ ভাঙে, ভাষা খেলায় নামে, কবিতা হয়ে ওঠে খণ্ডচিত্রের মতো অস্পষ্ট অথচ বোধসম্পন্ন।
উত্তরাধুনিক কবিতায় ভাষার নির্ভরযোগ্যতা আর নেই। একেকটি শব্দ বহন করে বহুমাত্রিক অর্থ। প্রতীক, চিত্রকল্প, আত্মবিদ্রুপ- সব মিলিয়ে তৈরি হয় কবিতার পোস্ট-স্ট্রাকচারাল টোন। এই সময়েই বাংলা কবিতায় প্রবেশ করে- নারীর দৃষ্টি, যৌনতা ও লিঙ্গচেতনা, বর্ণভিত্তিক বিদ্রোহ, জাতিগোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগণের কণ্ঠ।
কবিতা তখন আর শুধু শহুরে বুদ্ধিজীবীর নয়Ñ বরং আদিবাসী, নারী, রূপান্তরকামী, দিনমজুর- তাদেরও আত্মপাঠ। এক কবিতায় আরেক কবিতার প্রতিধ্বনি, পুরাণ ও রাজনৈতিক টেক্সটের ব্যবহার, ‘নির্মাণ’ ভেঙে ‘অস্বস্তি’ তৈরি করাই হয়ে ওঠে কবির কাজ।
এই অবস্থানই উত্তরাধুনিকতার সারকথাÑ চিরন্তনতা নেই, কেবল খণ্ড খণ্ড প্রতিফলন।
বাংলা কবিতা কখনোই একা ছিল না। যে কবি নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন, তার ভাষায়ও প্রবাহিত হয়েছে বিশ্ব-সাহিত্য, আন্দোলন, ফিলোসফি ও রীতির ছায়া। বিশ শতকের শুরুতে ইউরোপীয় আধুনিকতা যেমন বাংলা কবিতায় ঢুকে পড়ে, তেমনি পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার নিজস্ব স্বরও বিশ্ব সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙালি কবি যিনি বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তোলেন, আবার তা অতিক্রমও করেন। ড.ই. ইয়েটস তাকে অনুবাদ করেন, এবং তার গীতাঞ্জলীতে যে ঈশ্বরচিন্তাÑ তা যেন এক যোগসূত্র হয়ে ওঠে প্রাচ্য-প্রত্যয়ের মানবতাবাদী কাব্যধারার। টি. এস এলিয়টের দ্য ওয়াস্ট ল্যান্ড-এর মতোই জীবনানন্দের কবিতা ঘুরে ফিরে শহর, অস্থিরতা, মৃত্যুবোধ ও সময়ের স্তর নিয়ে কথা বলে। পাবলো নেরুদার রাজনৈতিক প্রেম ও বিপ্লবের ভাষা যেমন সাহসী, তেমনি আমরা সেটার সুর শুনতে পাই সুকান্ত, নজরুল, আল মাহমুদের উচ্চারণেও। বের্টল্ট ব্রেখটের নাট্যকবিতার দৃশ্যচিত্র বা শ্রেণিসংগ্রামের কবিতা বাংলার প্রগতিশীল কণ্ঠে অনুরণিত হয়।
পোস্টমডারিজমের যে বৈশ্বিক পটভূমি- ভাষার খেলা, সত্যের অনিশ্চয়তা, পাঠকের ভূমিকা, অন্তঃসরণ ও অন্তর্বিস্ফোরণ; বাংলা কবিতায় এগুলো নব্বই দশক থেকে স্পষ্টভাবে প্রবেশ করে।
এ সময় বাংলা কবিতা হয়ে পড়ে ‘পাঠ-নির্ভও পাঠ’- অর্থাৎ পাঠকের উপলব্ধিই হয়ে ওঠে কবিতার অর্থ।
আজ বাংলা কবিতা দু’টি বিপরীত স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে- একদিকে চিরায়ত কাব্যধারার ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাওয়া, অন্যদিকে নতুন মাধ্যম, নতুন কণ্ঠস্বর ও স্বাতন্ত্র্যবাদী কবিতার উত্থান।
কাগজে লেখা কবিতা আজ ডিজিটাল পর্দায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, ব্লগে, অডিওবুক বা ইউটিউব ভিডিওতে। ‘কবিতা এখন কাগজে নয়, স্ক্রলে চলে’Ñ এই বাস্তবতা পাল্টে দিয়েছে কবিতার অভিপ্রায়ও। তবে এতে গভীরতা কমে গেছে, নাকি প্রকাশের স্বাধীনতা বেড়েছেÑ এই বিতর্ক আজকের কবিতার বড় প্রশ্ন।
আধুনিক কবিরা আজ লিখছেন- নারীর শরীর ও মন নিয়ে, লিঙ্গ ও যৌনতা নিয়ে, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে, অস্তিত্ব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যুদ্ধ, অভিবাসন, ভাষাহীনতা নিয়ে। এইসব বিষয়ের অনুপস্থিতি একসময় কবিতার সীমাবদ্ধতা ছিল, আজ তা হয়ে উঠছে কবিতার স্বাধীন সত্তা।
তবু প্রশ্ন জাগে- কবিতা কি আজ পড়া হয়? না কি এটি নিজের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে? পাঠকসংখ্যার বিচারে কবিতা নিতান্তই সীমিত হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কবিতা মুহূর্তের গভীরতা ধারণ করেÑ যা কোনো মাধ্যম দিতে পারে না।
আজ বাংলা কবিতা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বা তার অবস্থানইবা কি এ প্রশ্ন উঠানোই যেতে পারে। বাংলা কবিতা এক দীর্ঘ ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহন করছে, যেখানে রয়েছে ধর্ম, বিদ্রোহ, প্রেম, শহর, গ্রাম, নিঃসঙ্গতা, শ্রেণিসংগ্রাম, পরমতা ও অনস্তিত্বÑ সব কিছুর সংমিশ্রণ। তবে হ্যাঁ আজ বাংলা কবিতা দাঁড়িয়ে আছে- নতুন কণ্ঠস্বর ও পুরাতন অভিজ্ঞতার সন্ধিক্ষণে; যেখানে অতীতকে ধারণ করেও সে ভিন্নভাবে ভাবতে চায়, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিকতাকে নিজের মতো করে আত্মস্থ করতে চায়। একথা বলা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হবে যে বাংলা কবিতা আজ নেই কোনো একমাত্র ধারায়- বরং তা বহুমুখী, বহুস্তর, বহুবাচক। এটি তারই প্রমাণ যে কবিতা এখনো প্রশ্ন তোলে, সম্ভাবনা খোঁজে এবং মানুষের আত্মার নিকটতম ভাষা হয়ে দাঁড়ায়।
পরিশেষে আলোচনার পরিসরে দাঁড়িয়ে বলা যায়- বাংলা কবিতা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল বা আছে- তার উত্তর একরৈখিক নয়, কিন্তু তা অনুপস্থিতও নয়। বাংলা কবিতা আজো জীবিত, কখনো গোপনে, কখনো দৃপ্ত কণ্ঠে, কখনো অন্ধকারে, কখনো আলোর প্রতীক্ষায়।
আজকালের খবর/আরইউ


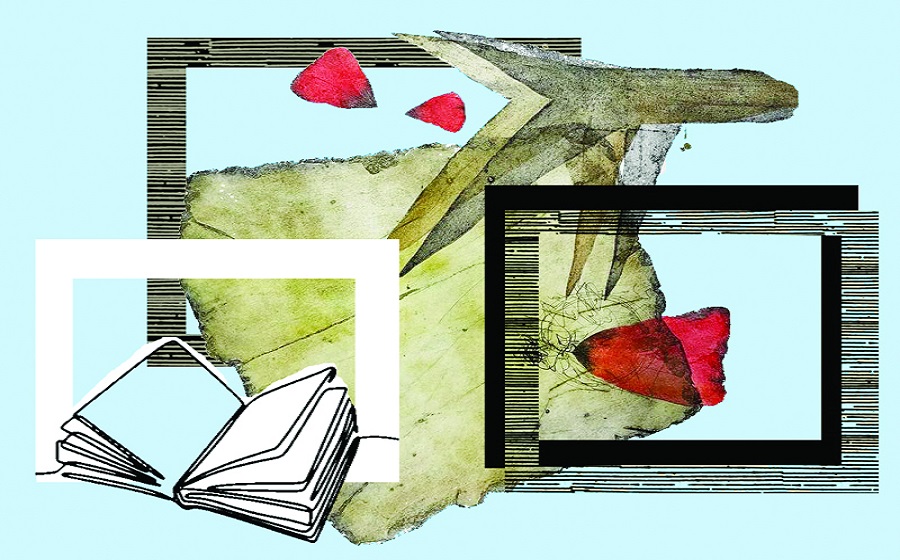 কবিতা কোনো ভাষার অলঙ্কারমাত্র নয়, বরং সেই ভাষার আত্মার সবচেয়ে সূক্ষ্ম, গভীর ও সংবেদনশীল প্রকাশ। বাংলা কবিতা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও বোধের নিগূঢ় নিঃশ্বাস। প্রশ্নটি তাই কেবল সাহিত্যিক নয়, আত্মজিজ্ঞাসার মতোÑ বাংলা কবিতা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, আর আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?
কবিতা কোনো ভাষার অলঙ্কারমাত্র নয়, বরং সেই ভাষার আত্মার সবচেয়ে সূক্ষ্ম, গভীর ও সংবেদনশীল প্রকাশ। বাংলা কবিতা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও বোধের নিগূঢ় নিঃশ্বাস। প্রশ্নটি তাই কেবল সাহিত্যিক নয়, আত্মজিজ্ঞাসার মতোÑ বাংলা কবিতা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, আর আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?